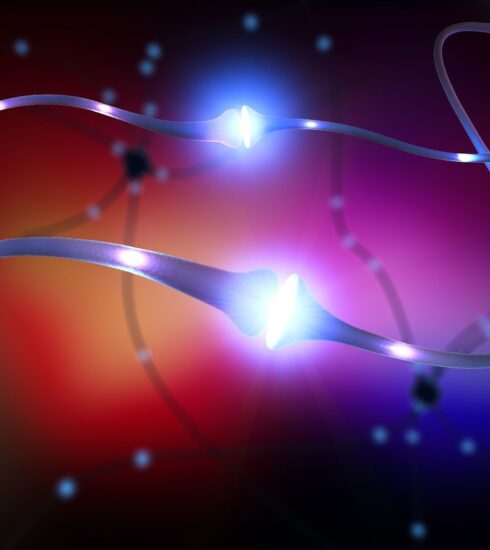কবর থেকে ভাইরাস
উনিশশো আঠেরো সালের ৭ সেপ্টেম্বর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন জোর কদমে। আমেরিকায় বস্টন শহরের অদূরে আর্মি ট্রেনিং ক্যাম্পের এক সেনা ঊর্ধ্বতন অফিসারকে জানাল, সে অসুস্থ। কী হয়েছে তার? প্রচণ্ড জ্বর। ব্যারাকের ডাক্তারবাবুরা সন্দেহ করলেন রোগটা মেনেঞ্জাইটিস। সে সন্দেহ পাল্টে গেল পরদিন। দেখা গেল, এক ডজন সেনাও ওই একই লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি। ১৬ সেপ্টেম্বর ভর্তি হল ৩৬ জন। ২৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ব্যারাকের মোট ৪৫,০০০ সেনার মধ্যে অসুস্থ ১১,৬০৪ জন। মহামারি। চলল প্রায় দেড় বছর। আক্রান্ত ব্যারাকের এক-তৃতীয়াংশ সেনা। মৃত্যু? প্রায় ৮০০ জনের।
যারা মারা গেল, তাদের চামড়া প্রায় নীলাভ। আর প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট। লক্ষণীয় ভাবে অবস্থার দ্রুত অবনতি। সকলের নয়, তবে যাদের মৃত্যু হল, তা এল সংক্রমণের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই। মৃতদেহের ময়নাতদন্তে দেখা গেল ফুসফুসে জমেছে তরল কিংবা রক্ত। চেনা রোগের এমন পরিণাম তো দেখা যায় না। এত বেশি পরিমাণে তো নয়ই। আমেরিকার মানুষ হতচকিত। চার দিকে ভয়ের বাতাবরণ। ঠিক যেমনটা কোভিড-১৯ নিয়ে আজ পৃথিবী জুড়ে।
অকস্মাৎ থাবা বসানো এই রোগকে এখনও গবেষকরা বলেন, ‘দ্য মাদার অব অল প্যানডেমিক্স’। সত্যিই তাকে অতিমারিদের মধ্যে রাজার আসনে বসানো যায়। ১৯১৮-র সেপ্টেম্বরে শুরু হয়ে চলল ১৯২০ অবধি। ছড়াল ইউরোপ তো বটেই, দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের আর্জেন্টিনা কিংবা এশিয়ার জাপানেও। মারা গেল মোট পাঁচ কোটি মানুষ। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা করলে যা আজকের হিসেবে ২০ কোটি দাঁড়াত।
সে সময়ে অতিমারির প্রকোপে পরিস্থিতি কেমন ছিল, তার বর্ণনা পাওয়া যায় ইতিহাসবিদ আলফ্রেড ডাবলু ক্রসবির লেখায়। হার্ভার্ড এবং ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসের এই অধ্যাপক তাঁর ‘আমেরিকা’স ফরগটেন প্যানডেমিক’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘‘নার্সরা প্রায়ই এমন এমন পরিস্থিতির শিকার হলেন যে, সে সবের তুলনা কেবল চতুর্দশ শতকের প্লেগ।’’ উদাহরণ দিয়ে ক্রসবি লিখলেন, ‘‘একজন নার্স একটি ঘরে ঢুকে দেখলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। যে ঘরে স্বামীর মৃতদেহ পড়ে আছে, সে ঘরে একটু দূরে তার স্ত্রী। পাশে তার সদ্যোজাত দুই যমজ শিশু। মৃত্যু এবং জন্ম দুই-ই ঘটেছে গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। হাতের কাছে পড়ে থাকা একটা আপেল ছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় কিছুই জোটেনি মহিলার।’’
বিশ্বযুদ্ধ তো ছিলই, তা ছাড়াও তখন দিনকাল আলাদা। ভাইরাস জিনিসটা মানুষের অপরিচিত না হলেও তাকে চোখে দেখা যায়নি। যে যন্ত্রের নাম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, তা তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। এমনি অণুবীক্ষণে যেখানে কোনও জিনিসকে দু’হাজার গুণ বড় করে দেখা যায়, সেখানে একটা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ কোনও জিনিসকে বড় করতে পারে এক কোটি গুণ। তাই সেই অণুবীক্ষণ তৈরি হওয়ার আগের যুগে ভাইরাস বস্তুটিকে দেখে ফেলার প্রশ্নই ওঠে না। সেই ভাইরাসের জিন? তা বিশ্লেষণ তো আরও দূরের কথা। আজ অবস্থা অন্য রকম। বিজ্ঞানীরা এখন ভাইরাসকে আলাদা করে দেখতে পারেন, তাঁর জিন বিশ্লেষণও করতে পারেন।
তখন আমেরিকার বিশিষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের এক জন উইলিয়াম হেনরি ওয়েল্ক। জনস হপকিন্স হাসপাতালের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। রোগটা কী, প্রশ্ন করায় তাঁর উত্তর : খুব সম্ভবত প্লেগই হবে। আর নয়তো নতুন কোনও রোগ, যার কথা এত দিন মানুষ শোনেনি। পরে বোঝা গেল, ও সব কিছু নয়। রোগটা নেহাতই ইনফ্লুয়েঞ্জা। হাজার হাজার বছরের পুরনো ব্যামো। নামটা অবশ্য নতুন। ইটালিয়ান। ইংরেজিতে যার প্রতিশব্দ ‘ইনফ্লুয়েন্স’। প্রভাব। ছোঁয়াচে বলে ও রকম নাম রোগটার। ইনফ্লুয়েঞ্জার চলতি নাম ফ্লু। জন এম ব্যারি রচিত ‘দ্য গ্রেট ইনফ্লুয়েঞ্জা’ বইয়ে দীর্ঘ বর্ণনা আছে ১৯১৮ সালের মড়কের। ওয়েল্ক ছাড়াও অন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা যে রোগটাকে চিনতে ভুল করেছিলেন, আছে সেই কাহিনিও।
যদিও প্রকোপ শুরু হয়েছিল আমেরিকায়, তবু ওই অতিমারি আজ পরিচিত স্প্যানিশ ফ্লু নামে। যেন তার শুরু স্পেন দেশে। নামের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক রাজনৈতিক ইতিহাস। তখন চলছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যুযুধান দেশগুলোর মধ্যে ছিল না স্পেন। তাই রোগের ক্ষয়ক্ষতি ও দেশের মিডিয়ায় প্রকাশিত হচ্ছিল সেন্সরশিপ ছাড়াই। যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলোয় খবর প্রচারিত হচ্ছিল রেখেঢেকে। স্পেনে তা হচ্ছিল না বলেই, লোকজন ধরে নিয়েছিল রোগের প্রকোপ বুঝি ওখানেই বেশি। সেই থেকেই নাম।
রেড ক্রসের তরফে যে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল তখন, তা এ রকম : ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধ করুন! কারও নিঃশ্বাসের সামনে দাঁড়াবেন না। মুখ ও দাঁত পরিষ্কার রাখুন। যারা কাশছেন বা হাঁচছেন, তাঁদের এড়িয়ে চলুন। যে সব জায়গার ভেন্টিলেশন কম, সে সব জায়গায় যাবেন না। গরম, নির্মল বাতাস এবং সূর্যালোকের মধ্যে থাকুন। নানা জন একই পানীয়ের কাপ বা তোয়ালে ব্যবহার করবেন না। হাঁচি বা কাশি হলে মুখে ঢাকা দিন। দুশ্চিন্তা, ভয় এবং ক্লান্তি থেকে দূরে থাকুন। ঠান্ডা লাগলে বাড়িতে থাকুন। কাজে বা অফিসে হেঁটে যান। অসুস্থ রোগীর ঘরে ঢোকার আগে মাস্ক পরে নিন।
তখন খবরের কাগজ ছিল আলাদা ধরনের। খবরের হেডলাইন বেরোত ধাপে ধাপে। এক খবরের অনেকগুলো হেডলাইন। ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’-এ প্রকাশিত এক খবরের হেডলাইন এ রকম : ‘ড্রাস্টিক স্টেপস টেকেন টু ফাইট ইনফ্লুয়েঞ্জা হিয়ার/ হেল্থ বোর্ড ইস্যুস ফোর পি এম ক্লোজ়িং অর্ডার্স ফর অল স্টোর্স এক্সেপ্ট ফুড অ্যান্ড ড্রাগ শপ্স/ আওয়ার্স ফর ফ্যাক্টরিজ় ফিক্সড/ প্ল্যান, ইন এফেক্ট টুডে, টু রিডিউস ক্রাউডিং অন ট্রান্সপোর্টেশন লাইন্স ইন রাশ পিরিয়ড্স/ টাইম টেবল ফর থিয়েটার্স/ র্যাডিকাল রেগুলেশন্স নেসেসারি টু প্রিভেন্ট শাটিং সিটি আপ টাইট, সেজ় ডক্টর কোপল্যান্ড।’
শিকাগো শহরের স্বাস্থ্য দফতর সাবধানতা প্রচারে ছাপাল পোস্টার। সাঁটল সিনেমা থিয়েটারের দেওয়ালে। পোস্টারে বড় বড় করে লেখা: ‘ইনফ্লুয়েঞ্জা/ প্রায়ই জটিল হয়ে যায়/ নিমুনিয়ার সঙ্গে/ এখন আমেরিকা জুড়ে/ এই থিয়েটার সহযোগিতা করছে স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে/ আপনি অবশ্যই তা করুন/ ঠান্ডা লাগলে, কাশলে এবং হাঁচলে এই হলে ঢুকবেন না/ বাড়ি যান, শুয়ে পড়ুন, যতক্ষণ না সুস্থ হয়ে উঠছেন/ কাশি, হাঁচি বা থুতু ফেলা এই হল-এ নিষিদ্ধ। যদি হাঁচি বা কাশি এসে যায়, তা হলে আপনার রুমাল ব্যবহার করুন। যদি তার পরও হাঁচি বা কাশি থাকে, তা হলে তৎক্ষণাৎ এই হল ছেড়ে চলে যান/ ইনফ্লুয়েঞ্জা সম্পর্কে সত্য জানাতে এবং জনগণকে শিক্ষিত করার কাজে এই থিয়েটার স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ/ শিকাগোকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর শহর হিসেবে গড়ে তুলতে আমাদের সাহায্য করুন/ জন ডিল রবার্টসন, স্বাস্থ্য কমিশনার।’
অ্যান্টিবায়োটিক তখনও আসেনি। ফলে রোগী মারা গেল অনেক। দেখা গেল মৃত্যুর আশু কারণ নিউমোনিয়া। আসল রোগ অন্য কিছু— ওই ইনফ্লুয়েঞ্জা। তা হলেও লোক মারা যাচ্ছে নিউমোনিয়ায়, যা ব্যাকটিরিয়া-ঘটিত। আর, ব্যাকটিরিয়ার সঙ্গে লড়াই করে অ্যান্টিবায়োটিক। তা আবিষ্কৃত হয়নি বলে, নিউমোনিয়া ঠেকানো যাচ্ছে না। আসলে ইনফ্লুয়েঞ্জা-আক্রান্ত মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ছে। দুর্বল শরীর নিয়ে নিউমোনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করা যাচ্ছে না। ফল, মৃত্যু। অনেক রোগের ক্ষেত্রেই এ রকম হয়। যেমন এডস। পুরো কথাটা হল, অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিশিয়েন্সি সিনড্রোম। জীবাণুর সংক্রমণে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এত কমে যায় যে, তখন জ্বর বা সামান্য ঘা-ও সারে না। এডস শরীরকে এতটাই দুর্বল করে তোলে। স্প্যানিশ ফ্লু-ও সে রকমই।
এক লাফে মানুষের গড় আয়ু নেমে এল আমেরিকায়। ১৯১৭ সালে তা ছিল ৫১ বছর। ১৯১৮ সালে দাঁড়াল ৩৯। তার আবার আর এক কারণ। স্প্যানিশ ফ্লু কোভিড-১৯’এর মতো নয়। কোভিড-১৯ মারছে সিনিয়র সিটিজ়েনদের। যারা এমনিতেই দুর্বল। সে জন্য কো-মর্বিডিটি (অন্য উপসর্গে মৃত্যু) এত বেশি। আর, ওই সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সিদেরই মেরেছিল বেশি। ওই বয়সের মানুষ টপাটপ মরে গেলে একটা দেশের গড় আয়ুষ্কাল তো ঝপ করে কমে যাবেই। ইনফ্লুয়েঞ্জায় ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সি মানুষ সাধারণত মারা যায় না। বুড়োরা কেন মারা গেল না, আর তরুণ যুবকরাই বা কেন মারা গেল? রোগটা যে হেতু ইনফ্লুয়েঞ্জা গোত্রের, আর ইনফ্লুয়েঞ্জা হরবখত হয়, তাই চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা দিলেন এ প্রশ্নের। বললেন, বয়স্করা জীবনে বহু বার ইনফ্লুয়েঞ্জার সম্মুখীন হয়েছেন। ফলে তারা ওই রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা অর্জন করেছেন। সেই ক্ষমতায় ওঁরা কাবু হন কম। অল্পবয়সিরা তা নয়। তাই প্রতিরোধ ক্ষমতা ওদের কম।
স্প্যানিশ ফ্লু-র ক্ষেত্রে সবচেয়ে আশ্চর্যের বোধহয় কেস ফেটালিটি রেট বা সিএফআর। যা ঘোরাফেরা করছিল ২.৫ থেকে ৫-এর মধ্যে। অর্থাৎ ১০০০ জন রোগে আক্রান্ত হলে, মারা গিয়েছিল ২৫ থেকে ৫০ জন। কোভিড-১৯’এর ক্ষেত্রে সিএফআর এখনও ওই পর্যায়ে পৌঁছয়নি। তবু স্প্যানিশ ফ্লু চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের হতবাক করে দিয়েছিল এই কারণে যে, এ ক্ষেত্রে সিএফআর ছিল সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রায় ৫০ গুণ!
এ হেন অতিমারির উৎস সন্ধানে বিজ্ঞানীরা আগ্রহী হবেনই। গবেষণায় প্রশ্নের উত্তর সহজে মেলে না। স্প্যানিশ ফ্লু যে এক ভাইরাসের কুকীর্তি, তা জানতে গড়িয়ে যায় এক দশকেরও বেশি। তার পর সেই ভাইরাসের খোঁজ। খোঁজ মানে, তা দেখতে কেমন, তার জিন উপাদান কী কী, ইত্যাদি। হ্যাঁ, সে সব জানতে কেটেছে আটটি দশক। দীর্ঘ প্রতীক্ষা!
কোথায় মিলবে সেই কালান্তক ফ্লু ভাইরাস? যা একদা বাসা বেঁধেছিল মানুষের ফুসফুসে? ১৯১৮-১৯১৯’এ মৃত মানুষের ফুসফুস চাই। কোথায় মিলবে তা? জানা গেল, উত্তর মেরুর কাছে আলাস্কায় আছে নাকি এক জেলেদের গ্রাম। ১৯১৮-র নভেম্বরে নাকি স্প্যানিশ ফ্লু মড়ক বাধিয়েছিল ওই গাঁয়ে। আশি জন মানুষের মধ্যে ৭২ জনই মারা গিয়েছিল ওই রোগে। মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে। তার পর? আর কী, বরফের পাহাড়ে গণকবর দেওয়া হল সেই ৭২টি মৃতদেহকে। বরফে চাপা মৃতদেহ। যেন ফ্রিজে রাখা খাবার। পচে-গলে নষ্ট হয়নি। আছে তাজা। অতএব, চলো আলাস্কার সেই গ্রামে। ফুসফুস খুঁজতে।
১৯৫১। গবেষকের দল গেলেন সেখানে। আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। দলের অন্যতম সদস্য স্নাতক স্তরের এক জন ছাত্র, সদ্য সুইডেন
থেকে আমেরিকায় পড়তে এসেছে। নাম জোহান হালটিন। তাঁর স্বপ্ন স্প্যানিশ ফ্লু-র মূলে থাকা ভাইরাসটিকে সে উদ্ধার করবে তুষার-কবরে ঢাকা মৃতদেহগুলি থেকে।
কবর খুঁড়ে বার করে আনা হল কয়েকটা মৃতদেহ। ৩৩ বছর আগের শব। তাদের ফুসফুসের টিস্যু পেতে কষ্ট হল না। কিন্তু, প্রচেষ্টা বিফল। ওই টিস্যু থেকে ল্যাবরেটরিতে ভাইরাস নতুন করে তৈরি করা গেল না। মনে রাখতে হবে, সালটা ১৯৫১। জীবরসায়ন গবেষণার প্রযুক্তি তখন উন্নত হয়নি।
স্প্যানিশ ফ্লু গবেষণায় আর কোনও অগ্রগতি হল না ৪৪ বছর। অবশেষে ১৯৯৫ সালে এলেন কিছু তরুণ বিজ্ঞানী। যেমন জেফ্রি টাউবেনবার্গার, অ্যান রিড, টমাস ফ্যানিং। চাকরিসূত্রে যাঁরা মেরিল্যান্ডের রকভিল-এ সামরিক বাহিনীর ইন্সটিটিউট অব প্যাথলজি-র সঙ্গে যুক্ত। ১৯৯৩ সালে মূলত টাউবেনবার্গারের উদ্যোগে গড়া হয় এক নতুন ল্যাবরেটরি। একেবারে আণবিক স্তরে ভাইরাস বা ব্যাকটিরিয়া নিয়ে কাজ করার জন্য। আরও ভাল করে বললে, জীবাণুর আরএনএ বা ডিএনএ নিয়ে কাজ করতে। যাতে ও সব শনাক্ত করে ভাইরাস বা ব্যাকটিরিয়াকে ভাল ভাবে চেনা যায়। এটা ‘রিডাকশনিজ়ম’। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ওই রিডাকশনিজ়ম-এর রণপায় ভর করে। রিডাকশনিজ়ম হল কোনও কিছুকে তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপাদানে ভেঙে ফেলা। লাভ? ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপাদানে ভেঙে ফেললে জিনিসের ধর্ম বুঝতে সুবিধে হয়। বায়োলজি তো আসলে কেমিস্ট্রি। আর কেমিস্ট্রি তো আসলে ফিজ়িক্স। বায়োলজিকে বুঝতে তাকে কেমিস্ট্রিতে ভেঙে ফেলা, কিংবা কেমিস্ট্রি বুঝতে তাকে ফিজ়িক্সে ভেঙে ফেলার নাম রিডাকশনিজ়ম। রোগজীবাণু হল বায়োলজি। তার চরিত্র বিশ্লেষণে তাকে কেমিস্ট্রিতে ভেঙে ফেলা জরুরি। মলিকুলার বায়োলজি বা আণবিক জীববিদ্যা ও ভাবে বায়োলজিকে কেমিস্ট্রিতে ভেঙে ফেলার শাস্ত্র। টাউবেনবার্গার, রিড এবং ফ্যানিং তিন জন যে হেতু মলিকুলার বায়োলজির গবেষক, তাই ওঁরা গড়ে তুললেন নতুন ল্যাবরেটরি। গবেষণাগার থাকলে আট দশক আগের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ভাইরাসের কণামাত্র পেলেই চলবে। আরএনএ ডিএনএ দিয়ে পুরোপুরি শনাক্ত হবে ভাইরাস।
ভাইরাস এ ভাবে শনাক্ত করার প্রক্রিয়া কাজে দেয় ১৯৯৪ সালে। মড়ক লেগেছিল ডলফিনদের। কারণ কী? মনে করা হয়েছিল, সমুদ্রতল থেকে উঠে আসা কোনও জীবাণু ওই মড়কের মূলে। ইনস্টিটিউট অব প্যাথলজি-র পরীক্ষায় বিশেষজ্ঞরা হাতে পেলেন ডলফিনের পচাগলা দেহ। তা-ই যথেষ্ট। ক্ষয়প্রাপ্ত টিস্যু থেকে আরএনএ সংগ্রহ করলেন বিশেষজ্ঞরা। জানা গেল, মড়কের মূলে এক ভাইরাস। কোন ভাইরাস? যা মানুষের দাঁতে হলুদ ছোপ ধরায়।
টাউবেনবার্গার, রিড এবং ফ্যানিং যে ইন্সটিটিউট অব প্যাথলজি গড়ে তোলেন, তা আসলে সামরিক বাহিনীর প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল মিউজ়িয়াম-এর উত্তরসূরি। ওই মিউজ়িয়াম গড়া হয়েছিল ১৮৬২ সালে। পরে ওই মিউজ়িয়ামে টিস্যু সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। তা জমতে জমতে পাহাড়। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ৩০ লক্ষ টিস্যু সংগৃহীত হয় ওই মিউজ়িয়ামে। তিন গবেষক খবর পান, ওই সংগ্রহের মধ্যে আছে স্প্যানিশ ফ্লু অতিমারির শিকারদের ফুসফুসের টিস্যু। থাকবেই, মিউজ়িয়াম যে সেনাবাহিনীর, আর মৃত্যুমিছিল যে শুরু হয়েছিল সেনাবিভাগেই। ওই তিন গবেষক ঠিক করলেন, উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে স্প্যানিশ ফ্লু-র ভাইরাসকে চিনবেন ওঁরা।
১৯১৮ সালে স্প্যানিশ ফ্লু-র কামড়ে মৃত মানুষদের ফুসফুস কেটে নিয়ে ফরম্যালডিহাইডে চুবিয়ে রাখা হত। বেছে বেছে ৭৮টা স্যাম্পল নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন টাউবেনবার্গার, রিড এবং ফ্যানিং। হঠাৎ ৭৮টা কেন? তিন গবেষক বাছলেন এমন স্যাম্পল, যেগুলো এসেছে এমন রোগীদের থেকে, যাঁরা মারা গেছেন দ্রুত। ভাইরাস ফুসফুস থেকে সরে পড়ে কয়েকদিনের মধ্যেই, তাই দ্রুত যাঁরা মারা যান তাঁদের ফুসফুসে ভাইরাস মেলার সম্ভাবনা বেশি। এক বছরের চেষ্টা— এবং অনেক ব্যর্থতার পর— কিছুটা সাফল্য। সাউথ ক্যারোলিনার ফোর্ট জ্যাকসন-এ ১৯১৮ সালে মৃত এক সেনার ফুসফুসে পাওয়া ভাইরাসের পাঁচটা জিনের গঠন কিছুটা জানা গেল ১৯৯৬ সালে। কিছুটা জানা মানে, তার মধ্যে অ্যাডিনিন, থাইমিন, সাইটোসিন এবং গুয়ানিন পর পর কী হিসেবে আছে, তা বুঝতে পারা। কিন্তু, ওই ক্রমান্বয় কি সত্যি স্প্যানিশ ফ্লু ভাইরাসের? না কি অন্য কিছুর? প্রশ্নের উত্তর জানতে পাওয়া চাই আর এক রোগীর ফুসফুস, যার ফুসফুস পরীক্ষা করলেও দেখা যাবে ওই ক্রমান্বয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পরের বছর ১৯৯৭ সালে পাওয়া গেল আর এক শবদেহ। আর এক সেনার। ১৯১৮-র সেপ্টেম্বরে— আগের সেনার মতো একই সময়ে— এই সেনাও মারা যান। অবশ্য অন্য এক ছাউনিতে, নিউ ইয়র্ক প্রদেশের ক্যাম্প আপটন-এ। পরীক্ষায় দেখা গেল, এই দ্বিতীয় সেনার ফুসফুসে জমে-থাকা ভাইরাসেরও কয়েকটা জিনেও অ্যাডিনিন, থাইমিন, সাইটোসিন আর গুয়ানিন একই ক্রমে রয়েছে। অর্থাৎ, একই ভাইরাস দুজন সেনার মৃত্যুর মূলে।
কিন্তু, তাতেও তো স্বস্তি মিলছে না। ও তো মাত্র কয়েকটা জিনের ক্রম। ভাইরাসের আরও জিন চেনা যে হল না। সে সব কি রয়ে যাবে অধরা? ওই চিন্তায় কাতর টাউবেনবার্গার, রিড এবং ফ্যানিং ভাবলেন, যতটুকু সাফল্য পাওয়া গিয়েছে, তা-ই বা কম কী। জার্নালে পেপার ছাপিয়ে ফেলা যাক। আরও দুই গবেষকের সঙ্গে ওঁরা লিখলেন পেপার। ছাপাল বিখ্যাত জার্নাল ‘সায়েন্স’। পেপারের শিরোনাম ‘ইনিশিয়াল জেনেটিক ক্যারেক্টারাইজ়েশন অব দি নাইন্টিন এইট্টিন স্প্যানিশ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস’। মাত্র চার পৃষ্ঠার প্রবন্ধ। তবু, তার সূত্রেই এল বড় সাফল্য। গবেষণায় কোনখান থেকে যে কী আসে, তা বলা মুশকিল।
‘সায়েন্স’-এ ছাপা ওই পেপার নজরে পড়ল এক জনের। জোহান হালটিন। একদা-ব্যর্থ গবেষক। ১৯৯৭ সালে তাঁর বয়স ৭৩। তিনি তখন এক অবসরপ্রাপ্ত প্যাথলজিস্ট। যৌবনে ব্যর্থতায় মনের দুঃখে পিএইচ ডি গবেষণা ত্যাগ করেছিলেন, বনে গিয়েছিলেন প্যাথলজিস্ট। সে চাকরি থেকেও অবসর নিয়েছেন কয়েক বছর আগে। এখন আর গবেষণা জগতের কোনও যোগাযোগ নেই। সেই মানুষ ‘সায়েন্স’ জার্নালে টাউবেনবার্গারদের লেখা পেপার পড়ে উৎসাহিত। চিঠি লিখলেন টাউবেনবার্গারকে। তিনি সাহায্য করতে প্রস্তুত। সুযোগ পেলে আরও এক বার ৪৬ বছর আগের গবেষণায় ফিরতে চান। নতুন পদ্ধতিতে গবেষণার সুযোগ আছে আলাস্কার সেই গ্রামে গণকবর খুঁড়ে পাওয়া ফুসফুস নিয়ে।
সাড়া দিলেন টাউবেনবার্গার। তিনি রাজি। হালটিন উৎফুল্ল। খোঁজ শুরু করলেন ১৯৫১-র সেই অভিযানের কোনও সদস্যের ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে কি না কবর খুঁড়ে পাওয়া ফুসফুসের টিস্যু। ৪৬ বছর আগের অভিযানের অনেক সদস্যই আর বেঁচে নেই। জীবিত এক সদস্যের কাছে ছিল টিস্যু, কিন্তু মাত্র এক বছর আগে ১৯৯৬ সালে তিনিও তা ‘আর কাজে লাগবে না’ ভেবে ফেলে দিয়েছেন। এখন উপায়?
গণকবর ফের খুঁড়তে হবে। বেঁকে বসলেন আলাস্কার সেই গ্রামের মানুষ। পূর্বজদের কবর তাঁরা খুঁড়তে দেবেন না। হালটিন গ্রামের নেতাদের বোঝালেন, গবেষণার স্বার্থে খনন জরুরি।
ওঁরা সে যুক্তি মানার পর গণকবর আবার খুঁড়লেন হালটিন, টাউবেনবার্গার এবং ওঁদের সহযোগীরা। অগস্ট, ১৯৯৭। ওঁরা পেলেন এক যুবতীর মৃতদেহ। যুবতী ছিলেন পৃথুলা। চর্বির পুরু আস্তরণ থাকায় তাঁর ফুসফুসের টিস্যু ছিল অটুট। সেই টিস্যু থেকে পরীক্ষায় মিলল স্প্যানিশ ফ্লু ভাইরাসের পুরো জিন মানচিত্র। ‘প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস’ জার্নালে ছাপা হল টাউবেনবার্গার, রিড, ফ্যানিং এবং হালটিন-এর লেখা পেপার— ‘ওরিজিন অ্যান্ড ইভলিউশন অব দ্য নাইন্টিন এইট্টিন স্প্যানিশ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস হিমাগ্লুটিনিন জিন’। ১৯৯৯। পরিচয় পাওয়া গেল ৮১ বছর আগে দাপিয়ে বেড়ানো এক ভাইরাসের।
যেন গল্পকথা! ঠিক যেমন গল্প ঘনাদার মুখে শোনার জন্য বসে থাকত ৭২ নম্বর বনমালী নস্কর লেনের লোকজন। বাস্তব এ ভাবেই বারবার প্রমাণ করেছে যে, সে সব রকম কল্পনার চেয়েও চমকপ্রদ।
আনন্দবাজার থেকে